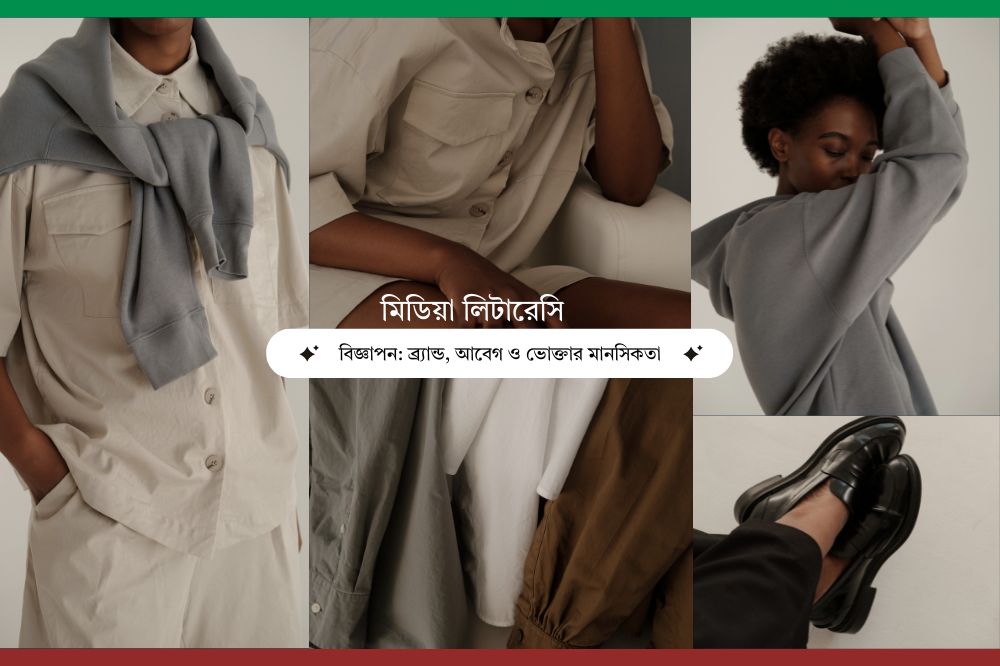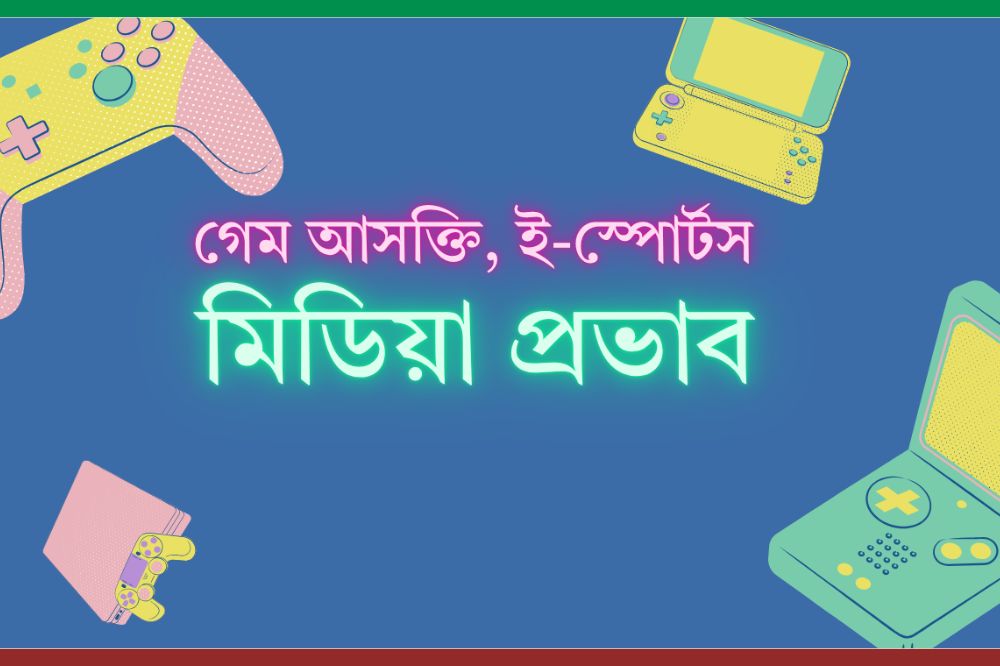| মিডিয়া লিটারেসি | মিডিয়া লিটারেসি
মালিকানা ও ক্ষমতা: গণমাধ্যমে পক্ষপাত ও জনমত নিয়ন্ত্রণ
৭ অক্টোবর ২০২৫
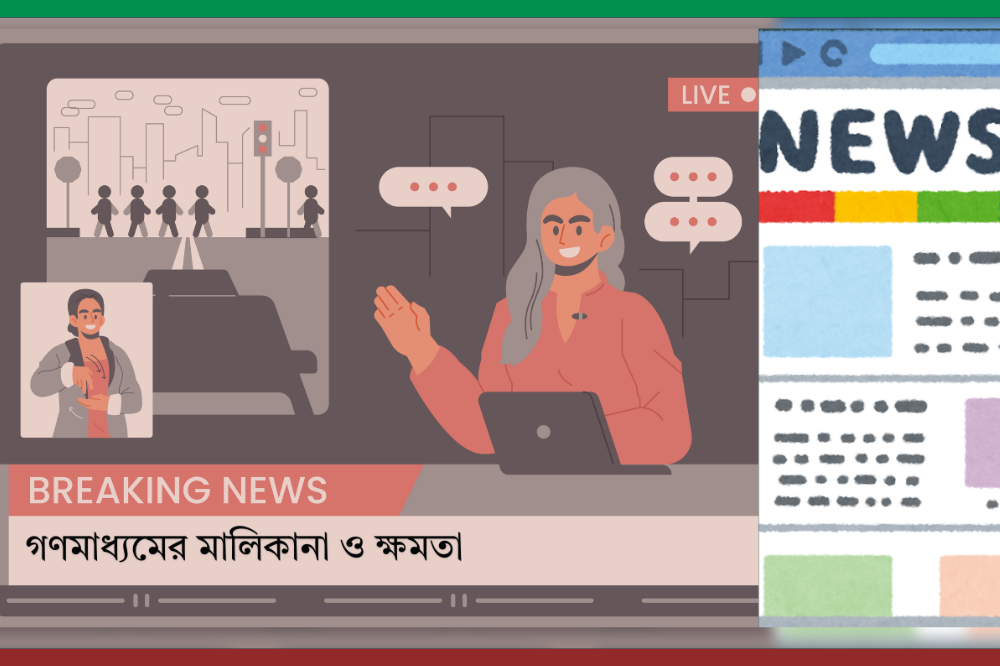
মালিকানা ও ক্ষমতা: গণমাধ্যমে পক্ষপাত ও জনমত নিয়ন্ত্রণ
গণমাধ্যম শুধু তথ্য ছড়ানোর মাধ্যম নয়, এটি ক্ষমতা প্রয়োগের হাতিয়ারও। যখন বড় কর্পোরেশন বা রাজনৈতিক স্বার্থান্বেষীরা মিডিয়ার মালিক হয়, তখন কনটেন্টের স্বাধীনতা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এর ফলে গণমাধ্যম অনেক সময় জনস্বার্থের পরিবর্তে মালিকদের এজেন্ডা পূরণ করে।
রাজনৈতিক দিক
বাংলাদেশে সংবাদপত্র, টেলিভিশন ও অনলাইন মিডিয়ার অনেক প্রতিষ্ঠান রাজনৈতিক দলের প্রভাবাধীন। ২০১৪ সালের নির্বাচনের সময় দেখা গেছে, অনেক চ্যানেল সরকারপন্থী খবর বেশি প্রচার করেছে, আর বিরোধী মতের সংবাদ কম প্রচার করেছে। ২০১৮ সালের ছাত্র আন্দোলনের সময় সোশ্যাল মিডিয়া বিকল্প প্ল্যাটফর্ম হিসেবে উঠে আসে, কারণ প্রচলিত গণমাধ্যমগুলো আন্দোলনের বাস্তব চিত্র পুরোপুরি দেখায়নি।
অর্থনৈতিক দিক
বড় ব্যবসায়ী ও কর্পোরেশন যারা মিডিয়া মালিক, তারা তাদের বাণিজ্যিক স্বার্থকে অগ্রাধিকার দেয়। এর ফলে ভোক্তা পণ্য, বিজ্ঞাপনদাতা বা কর্পোরেট ইমেজ ক্ষতিগ্রস্ত হবে এমন সংবাদ প্রায়ই বাদ পড়ে যায়। এতে মিডিয়ার বাণিজ্যিকীকরণ জনস্বার্থকে চাপা দিয়ে রাখে।
সামাজিক দিক
যখন মানুষ বুঝতে পারে যে মিডিয়া পক্ষপাতদুষ্ট, তখন তারা আস্থা হারায়। এর ফলে ভুয়া খবর বা সোশ্যাল মিডিয়া গুজব দ্রুত ছড়ায়, কারণ মানুষ বিকল্প উৎস খোঁজে। ২০২৪ সালের ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থান তার বড় প্রমাণ—প্রচলিত মিডিয়ার প্রতি অনাস্থা মানুষকে ফেসবুক-টুইটারের দিকে ঠেলে দিয়েছে।
গণমাধ্যমের মালিকানা যখন কিছু ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর হাতে সীমাবদ্ধ থাকে, তখন গণতন্ত্র হুমকির মুখে পড়ে। তাই স্বাধীন মিডিয়া আর মালিকানার স্বচ্ছতা জরুরি, যেন জনগণ প্রকৃত তথ্য পায়।
পরবর্তী বিষয়:
গণমাধ্যমের চোখে দর্শক: মানুষ নাকি পণ্য?
ভিডিও প্রতিবেদন দেখুন এখানে
আরও জানুন: মিডিয়া লিটারেসি ▶️ [প্লেলিস্ট লিঙ্ক]
Topics:

ভবিষ্যতের দায়িত্বশীল ব্যবহার: কেবল ভোক্তা নয়, বরং কনটেন্ট ক্রিয়েটর হিসেবেও নৈতিকভাবে মিডিয়া ব্যবহার করা
.jpg)
সমসাময়িক ইস্যু বিশ্লেষণ: ভুয়া খবর, প্রাইভেসি লঙ্ঘন, মিডিয়া ভায়োলেন্স ও খেলাধুলার কাভারেজ—নৈতিক ও সামাজিক প্রভাব
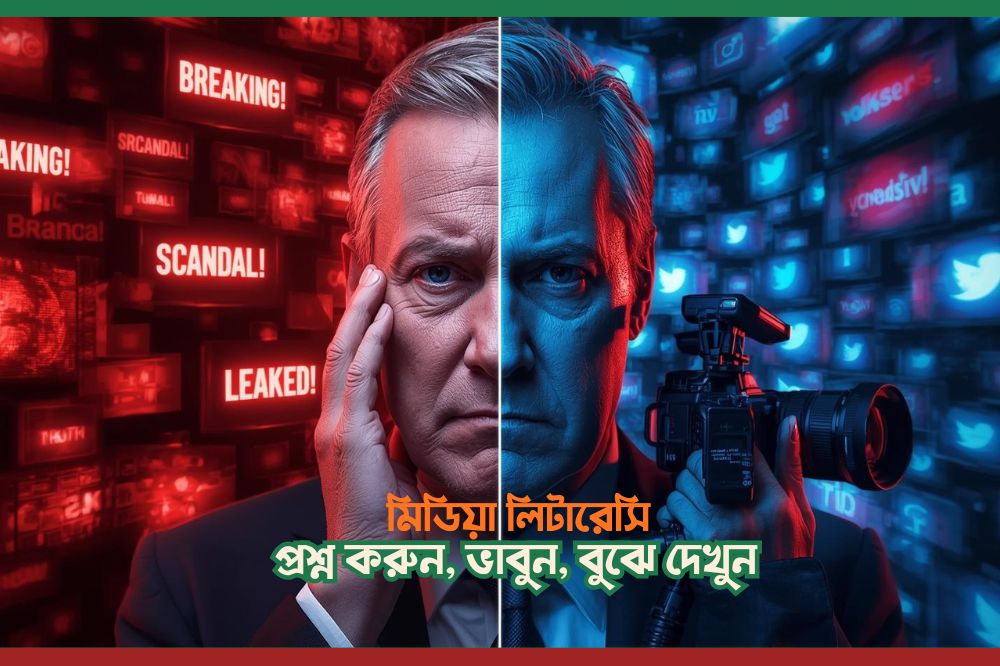
নিজেকে ও অন্যকে মিডিয়া লিটারেট করা: বিশ্লেষণ, প্রশ্ন, তুলনা ও সমালোচনামূলক চিন্তার অনুশীলন

ডিজিটাল এক্সপেরিয়েন্স: অনলাইন ভিডিও, মিউজিক, শপিং ও পাইরেসি—ভোক্তার আচরণ ও শিল্পের পরিবর্তন

সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং — ইকো-চেম্বার, ভুয়া প্রোফাইল, প্যারাসোশাল সম্পর্ক ও ব্যক্তিগত তথ্য শেয়ারের ঝুঁকি
আপনার মতামত দিন
এই পোস্টটি কি আপনার জন্য সহায়ক ছিল?
এখনো কেউ ভোট দেয়নি। আপনিই প্রথম হোন!
0%
0%
আপনার মতামত শেয়ার করুন:
| মন্তব্য সমূহ:
এখনও কোনো মন্তব্য নেই। প্রথম মন্তব্যটি করুন!

মিডিয়া লিটারেসি
মালিকানা ও ক্ষমতা: গণমাধ্যমে পক্ষপাত ও জনমত নিয়ন্ত্রণ
৭ অক্টোবর ২০২৫
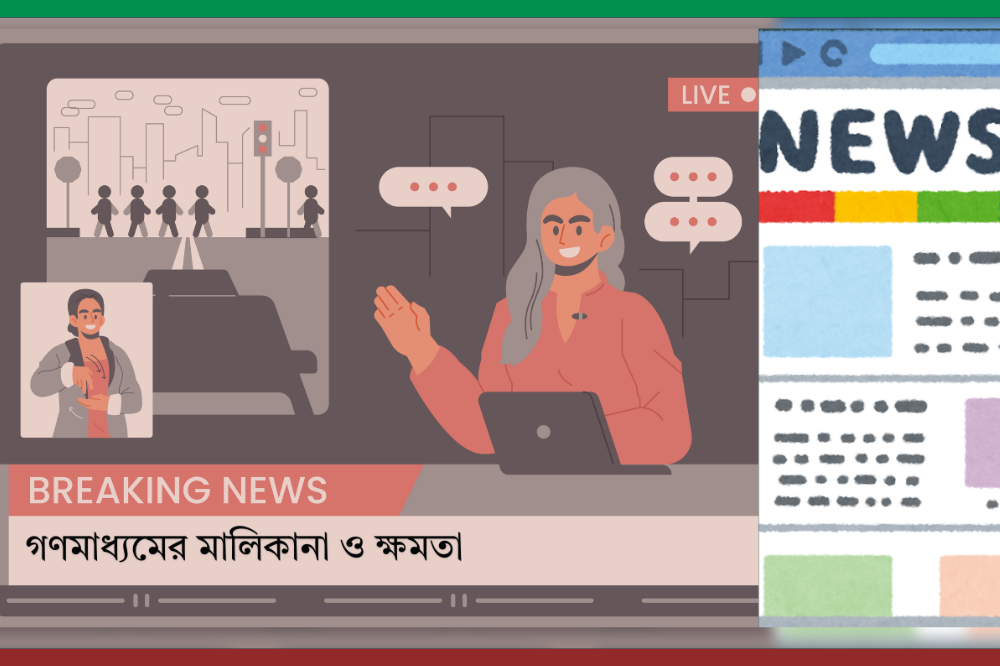
মালিকানা ও ক্ষমতা: গণমাধ্যমে পক্ষপাত ও জনমত নিয়ন্ত্রণ
গণমাধ্যম শুধু তথ্য ছড়ানোর মাধ্যম নয়, এটি ক্ষমতা প্রয়োগের হাতিয়ারও। যখন বড় কর্পোরেশন বা রাজনৈতিক স্বার্থান্বেষীরা মিডিয়ার মালিক হয়, তখন কনটেন্টের স্বাধীনতা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এর ফলে গণমাধ্যম অনেক সময় জনস্বার্থের পরিবর্তে মালিকদের এজেন্ডা পূরণ করে।
রাজনৈতিক দিক
বাংলাদেশে সংবাদপত্র, টেলিভিশন ও অনলাইন মিডিয়ার অনেক প্রতিষ্ঠান রাজনৈতিক দলের প্রভাবাধীন। ২০১৪ সালের নির্বাচনের সময় দেখা গেছে, অনেক চ্যানেল সরকারপন্থী খবর বেশি প্রচার করেছে, আর বিরোধী মতের সংবাদ কম প্রচার করেছে। ২০১৮ সালের ছাত্র আন্দোলনের সময় সোশ্যাল মিডিয়া বিকল্প প্ল্যাটফর্ম হিসেবে উঠে আসে, কারণ প্রচলিত গণমাধ্যমগুলো আন্দোলনের বাস্তব চিত্র পুরোপুরি দেখায়নি।
অর্থনৈতিক দিক
বড় ব্যবসায়ী ও কর্পোরেশন যারা মিডিয়া মালিক, তারা তাদের বাণিজ্যিক স্বার্থকে অগ্রাধিকার দেয়। এর ফলে ভোক্তা পণ্য, বিজ্ঞাপনদাতা বা কর্পোরেট ইমেজ ক্ষতিগ্রস্ত হবে এমন সংবাদ প্রায়ই বাদ পড়ে যায়। এতে মিডিয়ার বাণিজ্যিকীকরণ জনস্বার্থকে চাপা দিয়ে রাখে।
সামাজিক দিক
যখন মানুষ বুঝতে পারে যে মিডিয়া পক্ষপাতদুষ্ট, তখন তারা আস্থা হারায়। এর ফলে ভুয়া খবর বা সোশ্যাল মিডিয়া গুজব দ্রুত ছড়ায়, কারণ মানুষ বিকল্প উৎস খোঁজে। ২০২৪ সালের ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থান তার বড় প্রমাণ—প্রচলিত মিডিয়ার প্রতি অনাস্থা মানুষকে ফেসবুক-টুইটারের দিকে ঠেলে দিয়েছে।
গণমাধ্যমের মালিকানা যখন কিছু ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর হাতে সীমাবদ্ধ থাকে, তখন গণতন্ত্র হুমকির মুখে পড়ে। তাই স্বাধীন মিডিয়া আর মালিকানার স্বচ্ছতা জরুরি, যেন জনগণ প্রকৃত তথ্য পায়।
পরবর্তী বিষয়:
গণমাধ্যমের চোখে দর্শক: মানুষ নাকি পণ্য?
ভিডিও প্রতিবেদন দেখুন এখানে
আরও জানুন: মিডিয়া লিটারেসি ▶️ [প্লেলিস্ট লিঙ্ক]